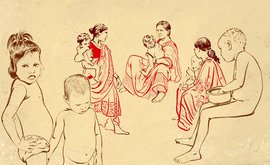হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার সময় দীপা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি যে তাঁর শরীরে একটি কপার-টি (এক প্রকার গর্ভনিরোধক যন্ত্র) ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।
সবে দ্বিতীয় সন্তান প্রসব করেছিলেন তিনি, এবারও ছেলে হয়েছে। তাঁর ইচ্ছে ছিল বন্ধ্যাত্বকরণ করিয়ে নেওয়ার, কিন্তু যেহেতু তাঁর সি-সেকশন করতে হয়েছিল, তাই "ডাক্তারবাবু বললেন যে দু-দুটো অপারেশন একসঙ্গে করা যাবে না," জানালেন দীপা।
তার বদলে ডাক্তার কপার-টিয়ের কথাটা পাড়েন, কিন্তু দীপা এবং তাঁর স্বামী নবীন (পরিচয় গোপন রাখতে দুজনেরই নাম পাল্টে দেওয়া হয়েছে) ভেবেছিলেন যে এটা নিছকই একটা পরামর্শ কেবল।
২০১৮ সালের মে মাসে তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন চারেক পর দিল্লির দীন দয়াল উপাধ্যায় (সরকারি) হাসপাতাল থেকে ছুটি পান দীপা। "ডাক্তারবাবু যে ইতিমধ্যেই ওর পেটের মধ্যে একটা কপার-টি গুঁজে দিয়েছে সেটা ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি," বলছিলেন নবীন।
দীপা কিংবা নবীন কেউই হাসপাতালের ডিসচার্জ রিপোর্ট পড়ে দেখেননি প্রথমটায়। হপ্তাখানেক পরে, ওঁদের মহল্লায় কর্মরত একজন আশাকর্মী সেসব কাগজপত্র খুঁটিয়ে না দেখলে কেউ জানতেও পারত না যে কী হয়েছে।
এই কপার-টি আসলে এক ধরনের গর্ভনিরোধক যন্ত্র (ইন্ট্রাইউটেরাইন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস – IUD) যেটিকে জরায়ুর মধ্যে স্থাপন করা হয়। "শরীরে এটা সড়গড় হতে হতে মাসের পর মাস কেটে যায়, অনেকেরই কষ্ট হয় খুব। তাই আমরা মহিলাদের বলে দিই যাতে তাঁরা নিয়মিত [টানা ছয়মাস] ডাক্তারখানায় এসে দেখিয়ে যান," জানালেন ৩৬ বছর বয়সী আশাকর্মী (অ্যাক্রেডিটেড সোশ্যাল হেল্থ অ্যাক্টিভিস্ট, স্বীকৃত সামাজিক স্বাস্থ্যকর্মী) সুশীলা দেবী। তিনি দীপাদের মহল্লায় ২০১৩ সাল থেকে কাজ করছেন।
তবে প্রথম তিনমাস শরীরে কোনও রকমের ব্যথা-বেদনা অনুভব করেননি দীপা। ওদিকে তাঁর বড়ো ছেলেও অসুস্থ ছিল, তাই সব মিলিয়ে ডাক্তারখানায় যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি তাঁর। বলতে গেলে একরকম মনস্থির করেই ফেলেছিলেন যে কপার-টি তিনি ব্যবহার করবেন।

পশ্চিম দিল্লিতে নিজের বাড়িতে দীপা: ছেলের শরীর খারাপ থাকায় ব্যস্ত ছিলেন, তাই মনস্থির করে ফেলেছিলেন যে কপার-টি তিনি ব্যবহার করবেন
এর ঠিক দুইবছর পর, ২০২০ সালের মে মাসে, ঋতুস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় অকল্পনীয় যন্ত্রণা।
বেশ কয়েকদিন যন্ত্রণা সহ্য করার পর দীপা বাধ্য হন তাঁর বাড়ি থেকে দুই কিলোমিটার দূরে দিল্লির বাক্কারওয়ালা এলাকার আম আদমি মহল্লা ক্লিনিকে (এএএমসি) যেতে। "ব্যথা কমার কয়েকটা ওষুধ দিয়েছিলেন ওখানকার ডাক্তারবাবু," বলছিলেন দীপা। একমাসেরও বেশি সময় ধরে তাঁকেই দেখিয়েছিলেন তিনি। "তাতেও যখন কষ্ট কমল না তখন উনি একজন মহিলা ডাক্তারের কাছে পাঠালেন আমাকে। বাক্কারওয়ালায় আরেকটা এএএমসি আছে, ইনি সেখানেই বসেন।"
তবে বাক্করওয়ালার যে এএএমসি-টায় দীপা প্রথমে গিয়েছিলেন, সেখানকার প্রধান চিকিৎসা আধিকারিক ডাঃ অশোক হংস কিন্তু দীপার কথাটা মনে করতে পারছিলেন না কিছুতেই – আসলে দিনে ২০০ জনেরও বেশি রোগী দেখতে হয় তো তাঁকে। "এই জাতীয় ঘটনায় আমরা চিকিৎসা করি বৈকি," আমাকে জানালেন তিনি, "ঋতুচক্রের কোনও গণ্ডগোল থাকলে চেষ্টা করি সেটা সারিয়ে তুলতে। নয়তো আমরা বলে দিই যে আলট্রাসাউন্ড করিয়ে অন্য কোনও সরকারি হাসপাতালে যেতে।" শেষমেশ সেই ক্লিনিকটি থেকে অবশ্য আলট্রাসাউন্ড পরীক্ষা করানোর কথা বলেছিল দীপাকে।
"উনি এসেছিলেন বটে, কিন্তু আমাকে শুধু ঋতুস্রাবের অনিয়মের কথা বলেছিলেন। সেটা শুনে আমি প্রথমে আয়রন আর ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খেতে বলি ওঁকে," জানালেন ডাঃ অমৃতা নাদার, বাক্কারওয়ালায় আরেকটা যে ছোট্টো এএএমসি আছে, ইনি সেখানেই কর্মরত। "কপার-টিয়ের ব্যাপারে তো কিছুই বলেননি প্রথমে। সেসব জানালে তো সঙ্গে সঙ্গে আলট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে খোঁজার চেষ্টা করতাম যে যন্ত্রটা শরীরের ঠিক কোনখানটায় ঢোকানো আছে। তার বদলে উনি একটা পুরোনো আলট্রাসাউন্ডের রিপোর্ট দেখিয়েছিলেন, সেটা দেখে মনে হয়েছিল যে সব ঠিকঠাকই আছে।" তবে দীপা কিন্তু হলফ করে বললেন যে তিনি কপার-টিয়ের কথা বলেছিলেন ডাক্তারকে।
২০২০ সালের মে মাসে ঋতুস্রাবের সঙ্গে যন্ত্রণা দিয়ে শুরু হয় তাঁর দীর্ঘ ভোগান্তির কাহিনি, সমস্যাগুলো উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে ক্রমশ। "আমার সাধারণত ওই দিন পাঁচেক পর রক্ত পরে বন্ধ হয়ে যেত, কিন্তু আস্তে আস্তে দেখলাম যে রক্তপাতটা বেড়েই চলেছে। জুন মাসে দশদিন রক্ত পড়েছিল। তারপরের মাসে সেটা বেড়ে হল পনেরো দিন। তারপর ১২ই অগস্টের পর থেকে যে ঋতুস্রাবটা শুরু হল, সেটা চলেছিল একটা গোটা মাস ধরে," বললেন দীপা।
পশ্চিম দিল্লির নাঙ্গলোই-নজফগড় সড়কের উপর দু-কামরার একটা পাকাবাড়িতে থাকেন দীপা, সেখানেই একটা কাঠের তক্তাপোষে বসে বসে বলছিলেন, "ওই ক'দিন এতো দুর্বল লাগছিল যে নড়তে চড়তে পারছিলাম না। মাথাটা সারাক্ষণ বনবন করছিল, কুটোটাও নাড়তে পারছিলাম না, খালি মনে হচ্ছিল যে শুয়ে থাকি। একেক সময় মনে হত কেউ যেন ধারালো কিছু একটা দিয়ে আমার তলপেটটা চিরে ফালাফালা করে দিচ্ছে। জামাকাপড় সব ভিজে যেতো রক্তে, সারাদিনে তাই বার চারেক কাপড় ছাড়তে হত। বিছানার চাদরটাদর সব ভিজে যা-তা অবস্থা হয়ে যেত।"

প্রেসক্রিপশন, ওষুধের রসিদ আর পরীক্ষার রিপোর্টের মাঝে দীপা এবং নবীন: 'পাঁচমাসে সাতটারও বেশি হাসপাতাল আর ডাক্তারখানার দ্বা রস্থ হয়েছি আমি'
২০২০ সালের জুলাই আর অগস্টে বাক্করওয়ালার ক্লিনিকটিতে দুবার গিয়েছিলেন দীপা। সেখানকার ডাক্তার দুবারই তাঁকে কিছু ট্যাবলেট খেতে দেন। "অনিয়মিত ঋতুস্রাবে যাঁরা আক্রান্ত, তাঁদের আমরা কয়েকটা ওষুধ দিই, আর বলি যে তাঁরা যেন ঋতুচক্রের হিসেব রাখেন। বুঝতেই তো পারছেন, এই ক্লিনিকে প্রাথমিক কিছু চিকিৎসা ছাড়া আর কিছুই সম্ভব নয়। আরও বিশদ পরীক্ষার নিরীক্ষার করতে হলে তাঁদের সরকারি হাসপাতালে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠাই," ডাঃ অমৃতা বলছিলেন আমায়।
ঠিক সেটাই করেছিলেন দীপা, অগস্ট ২০২০-এর মাঝ বরাবর বাস ধরে গিয়েছিলেন রঘুবীর নগরের গুরু গোবিন্দ সিং হাসপাতালে, সরকারি হাসপাতাল বলতে তাঁর বাড়ির সবচেয়ে কাছে এটিই (আনুমানিক ১২ কিমি দূরে)। সেখানকার ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে বিধান দেন যে তাঁর 'মেনোরেজিয়া' হয়েছে – অর্থাৎ ঋতুস্রাব চলাকালীন অতিরিক্ত সময় ধরে অস্বাভাবিক রকমের রক্তপাত।
দীপার কথায়, "এই হাসপাতালটার স্ত্রীরোগ বিভাগে দুইবার ঢুঁ মেরেছিলাম, যখনই গেছি তখনই তাঁরা দুই সপ্তাহের করে ওষুধ লিখে দিতেন। কিন্তু ব্যথা যে-কে-সেই রয়ে গেছিল।"
দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজনীতি নিয়ে বিএ পাশ করেছেন দীপা (২৪)। কাজের খোঁজে তাঁর মা-বাবা যখন সুদূর বিহারের মুজফফরপুর থেকে দেশের রাজধানীতে আসেন, দীপা তখন মোটে তিনমাসের। ছাপাখানায় কাজ করতেন তাঁর বাবা, এখন অবশ্য তিনি একটি মনিহারি দোকান চালান। দীপার স্বামী নবীন (২৯) কিন্তু আদতে রাজস্থানের দৌসা জেলার মানুষ। ক্লাস টুয়ের বেশি পড়াশোনা করতে পারেননি তিনি। ২০২০ সালের মার্চ মাসে লকডাউন শুরু হওয়ার আগে অবধি দিল্লির একটা স্কুল বাসে সহায়কের কাজ করতেন।
২০১৫ সালে বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই গর্ভবতী হয়ে পড়েন দীপা। সংসারের আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে তিনি মনস্থির করেছিলেন যে একটার বেশি বাচ্চা আসতে দেবেন না পরিবারে। কিন্তু তাঁর ছেলেটার দুমাস বয়সও হয়নি, তখন থেকেই বেচারা রোগভোগ করছে একটানা।
তিনি বলছিলেন, "বড়ো খোকার [পারসিস্টেন্ট] ডাবল্ নিউমোনিয়া আছে। একটা সময় গেছে যখন হাজার হাজার টাকা খরচ করেছি ওর চিকিৎসার পিছনে, ডাক্তাররা যা চাইত তা-ই দিয়ে দিতাম, একজন হাসপাতালের ডাক্তারবাবু তো মুখের উপর জবাব দিয়ে দিলেন, বললেন যে এ ছেলের বাঁচা মুশকিল। এটা শুনেই আমার পরিবারের লোকজন ঠিক করে যে আমাদের আরেকটা সন্তান আনা উচিত।"


একান্নবর্তী বাড়িতে এই দম্পতি যে কামরাটিতে থাকেন: 'সেই দিনগুলোয় এত দু র্বল লাগত যে নড়তে চড়তে পারতাম না। দু-পা হাঁটতে গেলেও দম ফেটে যেত। সারাক্ষণ মাথাটা বনবন করত, মনে হত যেন শুয়েই থাকি সারাদিন'
বিয়ের আগে কয়েকটা মাস একটা বেসরকারি প্রাথমিক ইস্কুলে পড়াতেন দীপা, বেতন ছিল ৫,০০০ টাকা। কিন্তু বড়ো ছেলের শারীরিক অবস্থা শেষ করে দেয় তাঁর শিক্ষকতার স্বপ্নকে।
সে ছেলের বয়েস আজ পাঁচ, মধ্য দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া (আরএমএল) হাসপাতালে বিনে পয়সায় চিকিৎসা করাতে দীপা তাকে তিনমাসে একবার করে নিয়ে যান বাসে চেপে। তবে কখনও কখনও দীপার ভাইয়ের বাইকে চেপেও যাতায়াত করেন তাঁরা।
সেরকমই একটা দিন, ২০২০ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর ছেলেকে নিয়ে আরএমএলে গিয়েছিলেন দীপা। আগে আগে হাজার একটা ক্লিনিক আর হাসপাতালে গিয়েও তো তাঁর অস্বাভাবিক ঋতুচক্রের কোনও কিনারা পাওয়া যায়নি, তাই ঠিক করলেন যে সেখানকার স্ত্রীরোগ বিভাগেই একবারটি দেখাবেন গিয়ে।
দীপা জানালেন, "[বিরামহীন যন্ত্রণার] কারণ বোঝার জন্য একটা আলট্রাসাউন্ড করল ওরা, তবে কিছুই তেমন খুঁজে পেল না, কপার-টি হন্যে হয়ে খুঁজেছিল ওখানকার ডাক্তার, কিন্তু হায়, পেল তো না-ই, উল্টে আবার সেই খানিক ওষুধপত্তর লিখে দিয়ে বলল ২-৩ মাস পর আসতে।"
অতিরিক্ত রক্তপাতের কারণ জানতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর আরেকজন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন দীপা। তাঁর পাড়ায় একখানা ছোট্টো বেসরকারি ক্লিনিক আছে, সেখানেই বসেন এই ডাক্তার। "এতোখানি রক্ত পড়ছে, তাও যে বেঁচে আছি এটা ভেবেই তাজ্জব বনে গেছিলেন তিনি। তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন, কিন্তু কপার-টি অধরাই থেকে গে'ল," বললেন তিনি। মাঝখান থেকে ২৫০ টাকা খসে গেল তাঁর। সেদিনই তাঁর এক আত্মীয় পরামর্শ দেন ৩০০টা টাকা দিয়ে প্রাইভেট ল্যাব থেকে তলপেটের (পেলভিস) এক্স-রে করাতে।
সেখানকার রিপোর্টে লেখা ছিল: 'দেখা যাচ্ছে যে শ্রোণীর একপাশে (হেমিপেলভিস) কপার-টি আটকে রয়েছে (ইন সিটু)'।


মাসের পর মাস তন্ন তন্ন করে খুঁজে শেষমেশ শ্রোণীর এক্স-রে করিয়ে পাওয়া গিয়েছিল সেই কপার-টি, সেটারই রিপোর্টখানা আশাকর্মী সুশীলা দেবীকে দেখাচ্ছেন দীপা
"সিজারিয়ান বা প্রসবের পরপরই কপার-টি শরীরে প্রস্থাপন করলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সেটা আপনাআপনি বেঁকে গেছে," জানালেন ডাঃ জ্যোৎস্না গুপ্তা, পশ্চিম দিল্লিতে কর্মরত একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। "তার কারণ প্রসবের পর জরায়ু স্ফীত অবস্থায় থাকে, যেটা স্বাভাবিক আয়তনে ফিরে যেতে বেশ খানিকটা সময় নেয়। আর সেটা হওয়ার সময় দেখা যায় যে কপার-টি ঘুরে বেঁকে গেছে। কোনও মহিলার যদি ঋতুস্রাব চলাকালীন অতিরিক্ত যন্ত্রণা হয় তখনও এমনটা হতে পারে।"
এমনটা আকছার হয়ে থাকে, জানালেন আশাকর্মী সুশীলা দেবী, "হামেশাই দেখি যে মহিলারা কপার-টির ব্যাপারে অভিযোগ করছেন। তাঁরা বলতে থাকেন যে ওগুলো তাঁদের 'পেটের ভিতর সেঁধিয়ে' গেছে, তাই অপারেশন করে বাদ দিতে হবে।"
জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৪ (২০১৫-১৬) জানাচ্ছে যে মোটে ১.৫ শতাংশ মহিলা গর্ভনিরোধক পন্থা হিসেবে আইইউডি পছন্দ করেন। অন্যদিকে ১৫-৪৯ বয়সী মহিলাদের মধ্যে ৩৬ শতাংশের পছন্দ বন্ধ্যাত্বকরণ অস্ত্রোপচার।
"অনেকের কাছেই শুনেছি যে কপার-টি তাদের সয় না, হাজার একটা গণ্ডগোল হয় এর থেকে," বলছিলেন দীপা, "কিন্তু দু-দুটো বছর তো আমার কোনও রকমের অসুবিধা হয়নি।"
আরও কয়েকটা মাস সেই অসহ্য যন্ত্রণা আর লাগামছাড়া রক্তক্ষরণ সহ্য করার পর গতবছর সেপ্টেম্বরে ভগবান মহাবীর হাসপাতালে যাবেন বলে ঠিক করেন দীপা। সরকারি এই সংস্থানটি উত্তর-পশ্চিম দিল্লির পিতম পুরায় অবস্থিত। ওখানকার নিরাপত্তা বিভাগে তাঁর এক আত্মীয় কাজ করতেন, দীপাকে তিনিই পরামর্শ দিয়েছিলেন সেখানে একজন ডাক্তারকে দেখাতে। তবে তার আগে কোভিড-১৯-এর জন্য পরীক্ষা করানো দরকার ছিল, তাই বাড়ির কাছেই একটা ডাক্তারখানায় যান তিনি।
সেই পরীক্ষায় দেখা যায় যে দীপা কোভিড পজিটিভ। অগত্যা দু সপ্তাহের জন্য ঘরে আটকা পড়লেন তিনি। যতক্ষণ না রিপোর্ট নেগেটিভ হচ্ছে ততক্ষণ শরীর থেকে কপার-টি বার করার জন্য কোনও হাসপাতালে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

'হামেশাই দেখি যে মহিলারা কপার-টির ব্যাপারে অভিযোগ করছেন,' জানালেন আশাকর্মী সুশীলা দেবী; কপার-টির কারণে হাজারটা ভোগান্তি তো ছিলই, তার উপর কোভিড-১৯ - এ আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন দীপা, তাই তাঁ র অক্সিজেন মাপতে এসেছেন সুশীলা দেবী
স্কুল বাসে কন্ডাক্টরের কাজ করতেন নবীন, মাস গেলে ৭,০০০ হাতে পেতেন, কিন্তু মার্চ ২০২০ নাগাদ দেশজুড়ে শুরু হয় লকডাউন, বন্ধ হয়ে যায় স্কুল-কলেজ সবকিছুই। ফলত কাজ হারিয়ে মাস পাঁচেক বেকার হয়ে বসে থাকতে বাধ্য হন বাড়িতে। এটাসেটা করে কেটেছে দিন, মাঝে কয়েকদিন স্থানীয় কয়েকজন ক্যাটেরারের সঙ্গেও কাজ করেছেন তিনি। এই কাজে দৈনিক ৫০০ টাকার বেশি জুটতো না কখনোই। (তারপর গতমাস, অর্থাৎ অগস্ট ২০২১-এ বাক্করওয়ালা মহল্লায় মূর্তি বানানোর একটা কারখানায় মাসিক পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে চাকরি পেয়েছেন নবীন।)
২৫শে সেপ্টেম্বর পরীক্ষা করিয়ে দীপা জানতে পারেন যে তিনি কোভিড নেগেটিভ, তারপর প্রতীক্ষা করে বসে থাকেন যে কবে ভগবান মহাবীর হাসপাতাল থেকে ডাক আসবে। ইতিমধ্যে এক আত্মীয় তাঁর সেই এক্স-রে রিপোর্টি নিয়ে ডাক্তারের কাছে যান – জবাব আসে যে মহাবীর হাসপাতালে কপার-টিয়ের ব্যাপারে কিছুই করা যাবে না, দীপাকে ফিরে যেতে হবে দীন দয়াল উপাধ্যায় হাসপাতালে (ডিডিইউ), অর্থাৎ ২০১৮ সালের মে মাসে যেখানে এই আইইউডি'টি তাঁর জরায়ুতে প্রতিস্থাপন হয়েছিল।
অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহটা কেটে যায় ডিডিইউ হাসপাতালের বহির্বিভাগে (আউট-পেশেন্ট ক্লিনিক) চক্কর কাটতে কাটতে। "ডাক্তারবাবুকে অনেক করে বললাম যাতে আমার শরীর থেকে কপার-টি বার করে বন্ধ্যাত্বকরণ করে দেয়। উনি তো মুখের উপর মানা করে দিলেন, বললেন যে কোভিড-১৯-এর কারণে হাসপাতালে নাকি আপতত এসব ধরনের অপারেশন বন্ধ আছে," মনে করে বললেন দীপা।
তাঁকে বলা হয় যে কোভিড কাটলে হাসপাতাল যখন আগের মতো আবার সব পরিষেবা দেওয়া শুরু করবে তখন বন্ধ্যাত্বকরণ আর কপার-টি বার করে আনা, দুটোই একসঙ্গে হয়ে যাবে।
আরও বেশ কতক ওষুধ লিখে দিয়েছিলেন ডাক্তার। "ডাক্তারবাবু বললেন কোনও রকমের অসুবিধা হলে ওনারা সেসব সামলাবেন, তবে ব্যাপারটা ওষুধ দিয়েই ঠিক হয়ে যাবে," গতবছর অক্টোবরের মাঝামাঝি নাগাদ জানিয়েছিলেন দীপা।
(প্রতিবেদক ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে ডিডিইউ হাসপাতালের বহির্বিভাগে গিয়েছিলেন দীপার ব্যাপারে বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে কথা বলতে, কিন্তু সেদিন তিনি কাজে আসেননি। তবে সেটার জন্য আমাকে নাকি মেডিক্যাল ডিরেক্টরের থেকে অনুমতি নিতে হবে, জানিয়েছিলেন অন্য একজন ডাক্তার। তা সেই ডিরেক্টরের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম বেশ অনেকবার, কিন্ত তাঁর তরফ থেকে একটাও জবাব আসেনি।)

'মনে তো হয়না উনি আদৌ কোনও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছিলেন বলে, [শরীর থেকে কপার-টি বার করার জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম]... 'দাইমা আমায় বলেন যে এটা বার করতে যদি আর কয়েকটা মাস দেরি করতাম, তাহলে হয়ত যমে-মানুষে টানাটানি শুরু হয়ে যেত'
"প্রতিটা সরকারি হাসপাতাল নাজেহাল হয়ে গিয়েছিল অতিমারি সামলাতে গিয়ে, গোটা শহরটাই তো তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল," দিল্লির পরিবার কল্যাণ অধিদপ্তরের (ডিরেক্টরেট অফ ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার) একজন প্রবীণ আধিকারিক জানালেন। "বেশ কয়েকটা হাসপাতালকে কোভিড হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হয়েছিল, তাই ওখানকার দৈনন্দিন পরিষেবা, এই যেমন ধরুন পরিবার পরিকল্পনা, এসব ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্ধ্যাত্বকরণের মতো চিরস্থায়ী প্রক্রিয়াগুলো থমকে দাঁড়ায়। তবে তার পাশাপাশি সাময়িক কিছু প্রক্রিয়ার লভ্যতা বেড়ে গিয়েছিল অনেকগুণ। মানুষ যাতে যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে পরিষেবাগুলো পায়, তার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা চালিয়েছিলাম আমরা।"
"গতবছর একটা লম্বা সময় জুড়ে পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সমস্ত পরিষেবা স্থগিত ছিল, কতজন যে এসে এসে ফিরে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই," জানালেন ডাঃ রেশমী আর্দেই, তিনি ভারতীয় প্রজনন স্বাস্থ্য পরিষেবার ফাউন্ডেশনের অধ্যক্ষ (ক্লিনিকাল সার্ভিস)। "এখন অবস্থার অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। এই পরিষেবাগুলো মানুষ যাতে আবারও পেতে পারে সেই ব্যাপারে সরকার বিবিধ নির্দেশ জারি করেছে। তবে হ্যাঁ, অতিমারির আগে যেমনটা ছিল, পরিস্থিতি ঠিক তেমনটা এখনও অবধি হয়ে ওঠেনি। নারী-স্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী।"
এ হেন পরিস্থিতির কারণে কী করবেন সেটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না দীপা। শেষে ১০ই অক্টোবর স্থানীয় এক দাইমার দারস্থ হন তিনি। ৩০০ টাকার বিনিময়ে সেই কপার-টি বার করে দেন তিনি।
দীপার কথায়, "মনে তো হয়না উনি আদৌ কোনও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছিলেন বলে [শরীর থেকে কপার-টি বার করার জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম]। হয়তো বা করেছিলেন, সঠিক জানি না। আমি তো চুপচাপ শুয়েছিলাম। তাঁর মেয়ে ডাক্তারি পড়ছে, তাই সে তার মায়ের কাজে হাত লাগিয়েছিল। দাইমা আমায় বলেন যে এটা বার করতে যদি আর কয়েকটা মাস দেরি করতাম, তাহলে হয়ত যমে-মানুষে টানাটানি শুরু হয়ে যেত।"
কপার-টি শরীর থেকে বার করে দেওয়ার পর থেকে অনিয়মিত ঋতুস্রাব এবং অতিরিক্ত রক্তপাত, এই দুটোই বন্ধ হয়ে গেছে তাঁর।
২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের একটা দিন, এযাবৎ যে যে হাসপাতাল এবং ডাক্তারখানার চৌকাঠ মাড়িয়েছেন, সেখানকার সমস্ত রসিদ আর প্রেসক্রিপশন খাটের উপরে জড়ো করতে করতে দীপা জানিয়েছিলেন: "এই পাঁচ মাসে সাতটারও বেশি হাসপাতাল আর ডাক্তারখানার দ্বারস্থ হয়েছি আমি।" সেটা করতে গিয়ে রাতদিন খেটে উনি এবং নবীন যেটুকু টাকা জমিয়েছিলেন তার সবটাই খরচা হয়ে গেছে।
তবে আর যে একটাও বাচ্চা জন্ম দেবেন না, এ ব্যাপারে তিনি বদ্ধপরিকর, তাই বন্ধ্যাত্বকরণ (টিউবাল লাইগেশন্) তিনি করাবেনই। এছাড়াও সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় বসতে চান দীপা। "[অ্যাপ্লিকেশন] ফর্মটা তুলেছি," জানালেন তিনি। সংসারের হাল ধরবার স্বপ্ন তাঁর বহুদিনের, অতিমারি এবং অভিশপ্ত সেই কপার-টিয়ের কারণে সেটা থমকে দাঁড়িয়েছিল। আজ নতুন উদ্যমে সেই স্বপ্নপূরণের পথে পা বাড়াতে তিনি উৎসুক হয়ে পড়েছেন।
পারি এবং কাউন্টার মিডিয়া ট্রাস্টের গ্রামীণ ভারতের কিশোরী এবং তরুণীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত দেশব্যাপী রিপোর্টিং প্রকল্পটি পপুলেশন ফাউন্ডেশন সমর্থিত একটি যৌথ উদ্যোগের অংশ যার লক্ষ্য প্রান্তনিবাসী এই মেয়েদের এবং সাধারণ মানুষের স্বর এবং যাপিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই অত্যন্ত জরুরি বিষয়টিকে ঘিরে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা।
নিবন্ধটি পুনঃপ্রকাশ করতে চাইলে zahra@ruralindiaonline.org – এই ইমেল আইডিতে লিখুন এবং সঙ্গে সিসি করুন namita@ruralindiaonline.org – এই আইডিতে ।
অনুবাদ: জশুয়া বোধিনেত্র (শুভঙ্কর দাস)